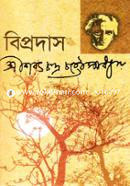একটু চোখ বুলিয়ে নিন
১
রমেশ এবার আইন-পরীক্ষায় যে পাস হইবে, সে সম্বন্ধে কাহারো কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাহার স্বর্ণপদ্মের পাপড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল দিয়া আসিয়াছেন– স্কলারশিপও কখনো ফাঁক যায় নাই।
পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ি যাইবার কথা । কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোনো উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ি আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ি যাইবে।
অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহাধ্যায়ী। পাশের বাড়িতেই সে থাকে । অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম । তাহার কন্যা হেমনলিনী এবার এফ. এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ি চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত।
হেমনলিনী স্নানের পর চুল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত । রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জন ছাদে চিলেকোঠার এক পাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে এরূপ স্থান অনুকূল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল।
এ পর্যন্ত বিবাহ সম্বন্ধে কোনো পক্ষ হইতে কোনো প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিস্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবূর মনে মনে লক্ষ্য আছে।
সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত । সে তর্ক তুলিয়াছিল যে পুরুষের বুদ্ধি খড়েগের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে পারে ; মেয়েদের বুদ্ধি কলম-কাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও-না কেন, তাহাতে কোনো বৃহৎ কাজ চলে না– ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগলভতা নীরবে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিকে খাটো করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি আনয়ন করিল। তখন রমেশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীজাতির স্তবগান করিতে আরম্ভ করিল।
এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্যদিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন সময় বেহারা তাহার হাতে এক-টুকরা চিঠি দিল । বহির্ভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা । চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপারটা কী রমেশ কহিল, “বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন। হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, “দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আনো-না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।”
রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, “না, আজ থাক্, আমি যাই।”
অক্ষয় মনে মনে খুশি হইয়া বলিয়া লইল, “এখানে খাইতে তাহাঁর হয়তো আপত্তি হইতে পারে।”
রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, “কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।”
রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “বিশেষ কোনো কাজ আছে কি?
ব্রজমোহন কহিলেন, “এমন কিছু গুরুতর নহে ।”
তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্য রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌত্হল-নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।
ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। ‘শ্রীচরণকমলেষু’ পর্যন্ত লিখিয়া লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, “আমি হেমনলিনী সম্বন্ধে যে অনুচ্চারিত সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোনোমতেই উচিত হইবে না।’
অনেকগুলা চিঠি অনেক রকম করিয়া লিখিল– সমস্তই সে ছিড়িয়া ফেলিল।
ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ির ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ির দিকে তাকাইয়া নিশাচরের মতো সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল।
রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল–রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল–রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে-বাড়ির কক্ষে কক্ষে সুগভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।
পরদিন ভোরের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহনবাবুর সতর্কতায় গাড়ি ফেল করিবার কোনোই সুযোগ উপস্থিত হইল না।
২
বাড়ি গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতি করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভালো ছিল না– ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশুকন্যাকে লইয়া দারিদ্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্যাটি আজ বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারই সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভালো নয় । ব্রজমোহন কহিলেন, “ও-সকল কথা আমি ভালো বুঝি না– মানুষ তো ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভালো দেখার বিচারটাই সর্বাগ্রে তুলিতে হইবে । মেয়েটির মা যেমন সতী-সাধী, মেয়েটিও যদি তেমনি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে।”
শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মতো ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনোটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সংকোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, “বাবা, এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি অন্যস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি ”
ব্রজমোহন। বল কী ! একেবারে পানপত্র হইয়া গেল?
রমেশ। না, ঠিক পানপত্র নয়, তবে–
ব্রজমোহন। কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?
রমেশ। না, কথাবার্তা যাহাকে বলে তাহা হয় নাই–
ব্রজমোহন। হয় নাই তো ! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর কণ্টা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে।
রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, “আর কোনো কন্যাকে আমার পতীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে”
ব্রজমোহন কহিলেন, “না-করা তোমার পক্ষে আরো বেশি অন্যায় হইতে পারে ”
রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাসিয়া যাইতে পারে।
রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে এক বৎসর অকাল ছিল– সে ভাবিয়াছিল, কোনোক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার এক বৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।
কন্যার বাড়ি নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে– নিতান্ত কাছে নহে– ছোটো বড়ো দুটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিন-চার দিন লাগিবার কথা । ব্রজমোহন দৈবের জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া এক সপ্তাহ পূর্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।
বরাবর বাতাস অনুকূল ছিল । শিমুলঘাটায় পৌছিতে পুরা তিন দিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো…..।
সম্পূর্ণ বইটি পড়তে চাইলে নিচের ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করে বইটি ডাউনলোড করে নিন।